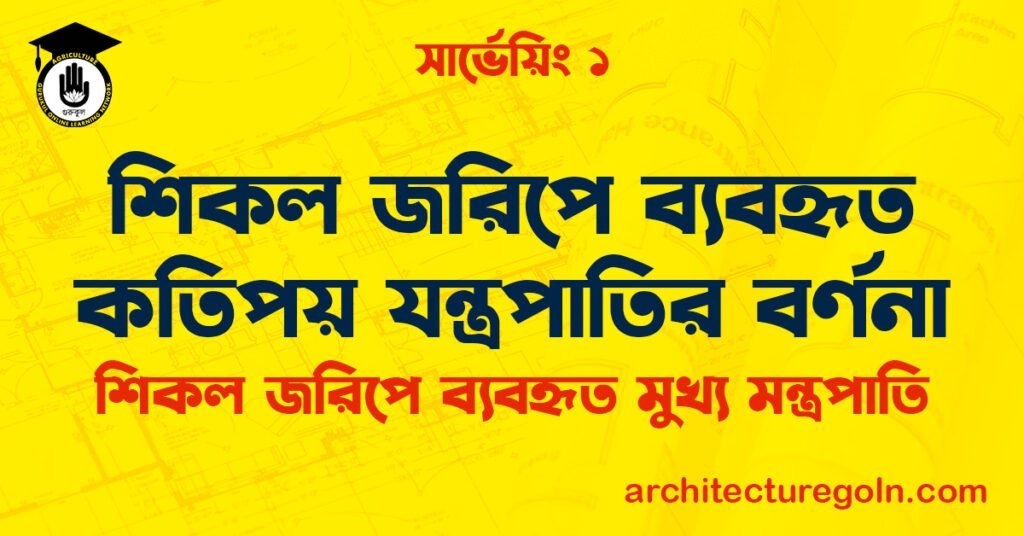শিকল জরিপে ব্যবহৃত কতিপয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “সার্ভেয়িং ১” এর “শিকল জরিপে ব্যবহৃত মুখ্য মন্ত্ৰপাতি” পাঠ এর অংশ।
Table of Contents
শিকল জরিপে ব্যবহৃত কতিপয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা
ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃত অবস্থান আপেক্ষিক উচ্চতা দিক, রৈখিক ও কৌনিক দূরত্ব পরিমাপের মাধ্যমে একটি স্কেল অনুসরণ করে সমতল কাগজে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে জরিপ বলে।
ক) গান্টার্স শিকল (Gunter’s chain) :
এডমন্ড গান্টার এ শিকলের আবিষ্কারক। এটা 66 ফুট লম্বা এবং 100টি সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের দৈর্ঘ্য 0.66 ফুট বা 7.92 ইঞ্চি, প্রতি ভাগকে এক লিঙ্ক (Link) বলা হয়। [চিত্র ঃ ৩.২ (ক)] শিকলটির প্রান্তদ্বয়ে দুটি হাতল আছে। হাতলের সাথে শিকলটি সুইভেল (Swivel) জোড়ায় সংযোজিত, যেন শিকলে মোচড় (Twist) না লাগে।
এক হাতলের প্রান্ত হতে অপর হাতলের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব সমান এক শিকল। শিকলটির অংশগুলো গ্যালভানাইজড্ মাইল্ড স্টিলের দণ্ডে তৈরি। এ শিকলে মাইল ও ফার্লং পরিমাপ করা সহজ (৪০ শিকল = 1 মাইল, 10 শিকল = 1 ফার্লং)। এ শিকল এ দেশে প্রচলিত চ ভূমি পরিমাপের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একর, শতাংশে জমির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা এ শিকলের 10 বর্গ শিকলে এক একর হয়। তাই এ সকল সুবিধার জন্য এ জাতীয় শিকল ভূমি জরিপকরগণ অধিক ব্যবহার করেন।
(খ) প্রকৌশল বা স্থপতি শিকল (Engineer’s chain) :
এ শিকল 100 ফুট লম্বা এবং 100 সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের দৈর্ঘ্য ৷ ফুট এবং প্রতি ভাগকে এক লিংক বলা হয়। [চিত্র ঃ ৩.২(খ)] এটার দু’প্রান্তে দু’টি হাতল থাকে। এক হাতলের প্রান্ত হতে অপর হাতলের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব সমান এক শিকল। এটার হাতলের জোড়া সুইভেল (Swivel) জোড়া। এটার দ্বারা দৈর্ঘ্যের পরিমাপ ফুটে এবং ক্ষেত্রফল বর্গফুটে নির্ণয় করা সহজ। এফ.পি.এস. (F.P.S) পদ্ধতির প্রচলন কালে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের পরিমাপে ব্যবহার করা হতো।
(গ) মিটার শিকল (Metre chain) :
এগুলো গ্যালভানাইজড মাইল্ড স্টিলের তারে তৈরি। তারের ব্যাস 4 মিমি। এ জাতীয় শিকল 20 ও 30 মিটার দৈর্ঘ্যের এবং যথাক্রমে 100 ও 150 ভাগে বিভক্ত । প্রতি ভাগকে লিঙ্ক (Link) বলা হয়। প্রতি লিঙ্কের দৈর্ঘ্য 200 মিমি, প্রতি মিটার পর পর (5, 10, 15 মিটার ব্যতীত) ব্রাসের তৈরি অতিরিক্ত একটি ছোট রিং এবং প্রতি 5 মিটার পর পর M অক্ষর অঙ্কিত একটি অতিরিক্ত রিং সম্বলিত ফুলি দেয়া থাকে। 25 মিটার দৈর্ঘ্যের শিকলও পাওয়া যায়, তবে প্রতি লিঙ্কের দৈর্ঘ্য 250 মিমি এবং 100 লিঙ্কে বিভক্ত।
শিকলের প্রত্যেকটি লিঙ্কের প্রান্ত ভাগে ফাঁসের মতো বাঁকানো অংশের সহিত বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার রিং সংযোগে সংযোজিত। এতে শিকলের নমনীয়তা (Flexibility) রক্ষা পায় এবং শিকল প্যাচ খাওয়া হতে নিষ্কৃতি পায় । যদি শিকলের লিঙ্কগুলোর জোড়াগুলো খোলা অবস্থায় থাকে তবে ওয়েল্ডিং করে নেয়া উত্তম।
এতে জোড়ার প্রসারণ ঘটতে পারে না এবং শিকলের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। শিকলকে টেনে নেয়ার জন্য এর উভয় প্রান্তে ব্রাসের তৈরি হাতল লাগান থাকে। এক হাতলের বহিঃপ্রান্ত হতে অপর হাতলের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বকে এক শিকল ধরা হয়। শিকলের হাতলদ্বয় সুইভেল জোড়ায় সংযোজিত। এতে শিকল মোচড় খাওয়া (Twist) হতে রক্ষা পায়। শিকলের এক লিংক বলতে দুটি ধারাবাহিক কেন্দ্রীয় রিং এর একটির কেন্দ্র হতে অপরটির কেন্দ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে বুঝায় । [চিত্র ঃ ৩.২(গ)]। প্রান্তীয় লিংকে হাতলের দৈর্ঘ্যও অন্তর্ভুক্ত।
হাতলের বহিঃপৃষ্ঠে তীর (Arrow) এর ব্যাসের অর্ধেক গভীরতায় গ্রুভ কাটা থাকে যেন প্রতি শিকল পর পর তীর বসালে কোনো ভ্রান্তি না আসে। শিকলের ফুলি বা ট্যাগ (tag)-গুলোতে দূরত্বের চিহ্ন দেয়া থাকে, যেন সহজেই পাঠ গ্রহণ করা যায়।সচরাচর ফুলির লেখা অথবা ফুলির দাঁতের সংখ্যা হতে সহজেই দূরত্বের পরিমাণ জানা যায়।
(ঘ) রেঞ্জিং রড (Ranging rod) :
রেঞ্জিং রড প্রধানত দু’ ধরনের কাজ করে থাকে। (১) স্টেশন বিন্দু চিহ্নিতকরণ ও (২) রেখাকে সোজাকরণ । এগুলো ভালোমানের সিজন করা (Seasoned) কাঠের তৈরি। সচরাচর সেগুন, শিশু, পাইন ও দেবদারু কাঠ দিয়ে রেঞ্জিং রড তৈরি করা হয়। এগুলোর প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার বা অষ্টভুজাকৃতির হয়ে থাকে এবং ব্যাস সাধারণত 3 সেমি। এগুলোর পোঁতা অংশের জন্য 15 সেমি দৈর্ঘ্যের লোহার নাল (Shoe) লাগানো হয়, যেন সহজে মাটিতে পোঁতা যায় এবং পোতার সময় ফেটে না যায়। এগুলো সচরাচর 2 বা 3 মি. লম্বা হয়ে থাকে এবং এগুলোতে 0.2 মি. দৈর্ঘ্যের দাগ দেয়া থাকে।
সহজে নজরে পড়ার জন্য দাগগুলোতে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি সাদা ও কালো অথবা লাল ও সাদা অথবা, লাল, সাদা, কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে দেয়া হয়। দূরত্ব অধিক হলে এগুলোর শীর্ষে 25 সেমি বর্গাকার পতাকা আটকে দেয়া হয় । পতাকা আটকে দেয়া রেঞ্জিং রড ঝাণ্ডি নামে পরিচিত।
(ঙ) ক্রস স্টাফ (Cross staff) :
কোনো বিন্দু হতে কোনো রেখার উপর লম্ব তৈরিকরণ অথবা কোনো রেখার কোনো নির্ধারিত বিন্দুতে লম্ব তৈরিকরণের জন্য ক্রস স্টাফ ব্যবহৃত হয়। এগুলো প্রধানত তিন ধরনের হতে পারে, যথা—(১) ওপেন ক্রস স্টাফ (Open cross staff) (২) ফ্রেন্স ক্রস স্টাফ (French cross staff) (৩) অ্যাডজাস্টেবল ক্রস স্টাফ (Adjustables cross staff) । এগুলোর মধ্যে ওপেন ক্রস স্টাফ (Open cross staff) সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এটা খুবই সাধারণ গঠনের। এটি দু’টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত, যথা—(১) ‘হেড’ (Head) ও (২) ‘লেগ’ (Leg) । এর ‘লেগ’টি মাটিতে পোঁতার জন্য ব্যবহৃত হয়।
‘হেড’টিতে দু’জোড়া চিত্রানুরূপ খাড়া লম্বা সরু ছিদ্র (Slit) থাকে এবং এদের সংযোজিত সরল রেখাদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। শিকল রেখার কোনো নির্ধারিত বিন্দুতে সমকোণ তৈরি করতে হলে প্রথমে ক্রস স্টাফটি ঐ বিন্দুতে ‘লেগ’ রেখে ঠিক উল্লম্বভাবে স্থাপন করে AB বা CD ছিদ্রপথে দৃষ্টিরেখা সামনের পোলের (Pole) সাথে মিলিয়ে নিতে হবে এবং অপর ছিদ্র দু’টি (যদি AB মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে CD ছিদ্র) দৃষ্টিরেখার সাথে মিলিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে পোল (Pole) পুঁততে হবে। এখন পোল ও শিকল রেখার নির্ধারিত বিন্দুর সংযোজিত রেখা শিকল রেখার উপর লম্ব হবে।
আর যদি শিকল রেখার উপর কোনো নির্ধারিত বস্তু বা বিন্দু হতে লম্ব ফেলতে হয় তবে শিকল রেখার উপর ক্রস স্টাটি আগে- পিছে করে যে বিন্দুতে এক জোড়া ছিদ্রের (ধরি AB) দৃষ্টিরেখা শিকল রেখার সাথে এবং অপর জোড়া (CD) ছিদ্রের দৃষ্টিরেখা নির্ধারিত বস্তু বা বিন্দুর সাথে মিলে যাবে। শিকল রেখার ঐ বিন্দুতেই এ নির্ধারিত বস্তু বা বিন্দু লম্ব উৎপন্ন করবে।
ফ্রেন্স ক্রস স্টাফ :
এটা অষ্টভুজাকৃতির ফাঁপা বাক্সবিশেষ [চিত্র ঃ ৩.২(ছ)]। এ বাক্সের খাড়া প্রতি তলের মাঝখানে একটি করে খাড়া ছিদ্র (Slit) থাকে। এতে বিপরীত দিকের ছিদ্রদ্বয়ের সংযোজিত রেখা পরস্পরের সাথে 45° কোণ সৃষ্টি করে। এগুলোর সাহায্যে শিকল রেখার সাথে 45° ও 90° কোণ তৈরি করা যায়।
অ্যাডজাস্টেবল ক্রস স্টাফ :
একটির উপর আরেকটি স্থাপিত এরূপ দু’টি সমব্যাসের সিলিন্ডারের সমন্বয়ে এটি তৈরি [চিত্র ঃ ৩.২(জ)]। উভয়টিতে দৃষ্টিরেখার জন্য ছিদ্র থাকে। উপরে সিলিন্ডারে চিত্রানুরূপ একটি ভার্নিয়ার থাকে এবং নিচেরটির সাথে আপেক্ষিকতা বজায় রেখে ‘মিল হেডেড ‘স্ক্রু এর সাহায্যে এটাকে ঘুরানো যায়। নিচের সিলিন্ডারটিতে ডিগ্রি ও ডিগ্রি অংশের দাগকাটা থাকে । তাই এটার সাহায্যে শিকল রেখার সাথে যে-কোনো কোণ তৈরি করা যায় । ক্রস স্টাফসমূহের দ্বারা তৈরি লম্ব ততটা সঠিক নয়। সঠিক লম্ব তৈরির জন্য অপটিক্যাল স্কয়ার ব্যবহার করাই উত্তম।
(চ) অফসেট রড (Offset rod) ঃ
এগুলো রেঞ্জিং রডের মতো এবং 3 মিটার লম্বা। এগুলোতেও 0.2 মিটার দৈর্ঘ্যের দাগ দেয়া থাকে এবং রেঞ্জিং রডের মতো রং করে দেয়া হয়। তবে এদের মাথায় আংটা লাগানো থাকে যেন বেড়া বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকের ছিদ্রপথে শিকলকে আংটায় ( hook) আটকিয়ে টেনে বা ঠেলে নেয়া যায়। এগুলোতে চক্ষু উচ্চতায় পরস্পর সমকোণে (দৈর্ঘ্য বরাবর) ছিদ্র লাল বা কালো ব্যান্ড করা থাকে। এতে অফসেট (offset) লাইন সংস্থাপনে সুবিধা হয়। ছোটখাটো অফসেট পরিমাপের ক্ষেত্রেও এগুলো ব্যবহার করা যায়। রেঞ্জিং রড ও অফসেট রড যদিও দেখতে একই রকম, তবুও এ দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে রেঞ্জিং রড ও অফসেট রডের পার্থক্য দেয়া হলো :
(ছ) ওলন (Plumb-bob) :
ধাপ পদ্ধতিতে পাহাড়িয়া অঞ্চলে শিকল জরিপের সময় ওলন ব্যবহৃত হয় [চিত্র ঃ ৩.২ (ঞ)]। থিওডোলাইট বা এ ধরনের জরিপে ভূমিতে স্টেশন বিন্দুর অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও রেঞ্জিং রড উল্লম্বভাবে স্থাপনের জন্যে ওলন ব্যবহৃত হয়।
(জ) তীর (Arrow) ঃ
এগুলো শক্ত ইস্পাতের তারের তৈরি [চিত্র ঃ ৩.২(ট)]। এগুলোকে মার্কিং পিন বা চেইনিং পিন (Marking pin or chaining pin)-ও বলা হয়। সাধারণত একটি শিকলের সাথে 10টি তীর সরবরাহ করা হয়।
এগুলো তৈরিতে ব্যবহৃত তারের ব্যাস 4 মিমি হয়ে থাকে এবং এগুলো কালো রঙের এনামেল (Enamel) করা থাকে। তীরের দৈর্ঘ্য 250-500 মিমি হয়ে থাকে। সচরাচর ব্যবহৃত তীরের দৈর্ঘ্য 400 মিমি। এগুলোর এক প্রান্ত সুচালো থাকে যেন সহজে মাটিতে পোতা যায় এবং অপর প্রান্ত চিত্রানুরূপ ফাঁসের মতো যেন সহজে বহন করা যায়। শক্ত মাটিতে দাগ কাটার জন্যও তীরের সুচালো প্রান্ত ব্যবহার করা যায়।
(ঝ) টেপ (Tapes) ঃ
টেপ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীতে তৈরি করা হয়। তবে নিচের পাঁচ শ্রেণির টেপই প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ
১। কাপড় বা লিনেন টেপ (Cloth or linen tape )
২। ধাতব টেপ (Metallic tape ) ৩। ইস্পাত টেপ (Steel tape )
৪ । ইনভার টেপ (Invar tape )
৫। ফাইবার গ্লাসের ফিতা (Fiber glass tape
১। কাপড় বা লিনেনের টেপ :
12 হতে 15 মিমি চওড়া ভালো বুননের কাপড় বা লিলেনের কাপড়ে বার্নিশ করে এ ধরনের টেপ তৈরি করা হয়। এগুলো হালকা, আর্দ্রতারোধী ও নমনীয় (Flexible)। সাহায্যকারী বা অপ্রধান পরিমাপ যেমন অফসেট (offset) J নেয়ায় এগুলো ব্যবহৃত হয়। কাপড়ের টেপ 10 মিটার, 20 মিটার, 25 মিটার ও 30 মিটার দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে (33 ফুট, 66 ফুট ও 100 ফুটেরও হতে পারে)। টেপের প্রান্তে ব্রাসের রিং সংযুক্ত থাকে এবং রিংয়ের দৈর্ঘ্য সমেত টেপের দৈর্ঘ্য ধরা হয়। কাপড়ের টেপ সূক্ষ্ম পরিমাণের জন্য নিম্নোক্ত কারণে খুব কমই ব্যবহৃত হয়।
কারণগুলো হচ্ছে—(১) এগুলো আর্দ্রতায় আক্রান্ত হয় এবং সঙ্কুচিত হয় (২) টানের উপর এর দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে (৩) এগুলোতে জট বা পাক লেগে যেতে পারে ও (৪) এগুলো শক্তিশালী নয় । এগুলো শুষ্ক ও পরিষ্কার করে রিল (Reel)-এ গুটানো উচিত। [চিত্র ঃ ৩.২(ঠ)]
২। ধাতব টেপ :
এগুলো যাতে টানে সহজে লম্বা না হয় তজ্জন্য কাপড় বা নাইলনের টেপের সাথে পিতল বা তামার সূক্ষ্ম তারের বুনন দেয়া হয়। এগুলো কাপড় বা নাইলনের টেপের তুলনায় ভালো। তবে এগুলোও সাহায্যকারী পরিমাপে যেমন অফসেট নেয়ায় ব্যবহৃত হয়। এগুলো চামড়ার কেইসে গুটিয়ে রাখা হয়। এগুলোর দৈর্ঘ্য সাধারণত 2 মিটার, 5 মিটার, 10 মিটার, 20 মিটার, 30 মিটার ও 50 মিটার হয়ে থাকে। এগুলোতে সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার ও মিটারে দাগকাটা থাকে ।
৩। ইস্পাত টেপ :
এগুলো 1 মিটার, 2 মিটার, 10 মিটার, 30 মিটার ও 50 মিটার দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এগুলো ইস্পাত বা মরিচারোধী ইস্পাতে তৈরি। এগুলোর বাইরের দিকের প্রান্তে রিং বা অন্য কোনো ডিভাইস সংযুক্ত করে দেয়া হয় যেন সহজে টেনে বের করা যায়। টেপের দৈর্ঘ্য রিং এর দৈর্ঘ্য সমেত হিসেব করা হয়। এ জাতীয় টেপের দু’প্রান্তীয় অংশে মিলিমিটারের দাগসহ পুরো টেপে সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার ও মিটারের দাগ দেয়া থাকে।
এ জাতীয় টেপ কেইসে (Case) গুটানোর কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। নিখুঁত মাপের ক্ষেত্রে এ জাতীয় টেপ ব্যবহার করা যায়। এগুলো সহজেই পাক লেগে কেটে যেতে পারে। তাই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হয় এবং ব্যবহারের পর মুছে পরিষ্কার করে তেল বা গ্রিজ লাগিয়ে রাখতে হয়।
৪। ইনভার টেপ :
নিখুঁত ও সূক্ষ্ম দৈর্ঘীয় পরিমাপের জন্য ইনভার টেপ ব্যবহার করা হয়। বিশেষত ত্রিভুজায়ন জরিপের ভিত্তি রেখার পরিমাপে এ জাতীয় টেপ ব্যবহৃত হয়। ইনভার টেপ নিকেল (36%) ও ইস্পাতের সংকর ধাতুতে তৈরি করা হয়। এগুলোর দৈর্ঘীয় তাপীয় প্রসারাঙ্ক খুবই কম, প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য 0.63 X 10″। এগুলো 6 মিলিমিটার চওড়া এবং এগুলোর দৈর্ঘ্য 30 মিটার, 50 মিটার ও 100 মিটার হতে পারে।
এগুলোর পুরো দৈর্ঘ্যে দাগ দেয়া থাকে না, মাত্র উভয় প্রান্তে । মিটার করে 10 মিটার পর্যন্ত দাগ দেয়া থাকে। এগুলো বেশ ব্যয়বহুল, ইস্পাতের তুলনায় সহজেই বিকৃত হয় এবং সময়ের সাথে এগুলোতে ক্রীপ (Creep) দেখা দেয়। এদের তাপীয় প্রসারাঙ্কের মাত্রা পরিবর্তনশীল। তাই সময় সময় এগুলোর দৈর্ঘ্য এবং তাপীয় প্রসারাঙ্ক যাচাই করে নিতে হয়। এগুলো সহজে বেঁকে যায় এবং বিনষ্ট হয়। তাই এগুলোকে বৃহৎ ব্যাসের রীলে গুটাতে হয়। এগুলো সাধারণ কাজে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত 50 সেন্টিমিটার ব্যাসের রিলে এগুলো গুটানো হয়ে থাকে।
৫। ফাইবার গ্লাস ফিতা :
ফাইবার গ্লাসে পিভিসি (PVC) কোটিং দেয়া। এ জাতীয় ফিতাগুলো 30 মিটার দৈর্ঘ্যের এবং প্রতি মিটারকে 10 ভাগে ভাগ করা থাকে। আবার প্রতি ভাগকে 10 ভাগ করা অর্থাৎ প্রতি ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য 1 সেন্টিমিটার। প্রতি 10 ভাগ পর পর সংখ্যা মান লেখা থাকে। এটা দেখতে অনেকটা ধাতব ফিতার মতো ।
(ঞ) অপটিক্যাল স্কয়ার (Optical Square) ও অপটিক্যাল প্রিজম স্কয়ার :
অপটিক্যাল স্কয়ার একটি সাধারণ গঠনের ছোট যন্ত্র । বৃত্তাকার বা অনেকটা গোঁজ আকৃতির, ধাতব পাতে নির্মিত বক্সে দুটি আয়না পরস্পর 45° কোণে স্থাপন করে এটি তৈরি করা হয়। শিকল জরিপে শিকল রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব স্থাপনে বা কোনো বস্তু হতে শিকল রেখার লম্ব পাদমূল বিন্দু নির্ধারণে এটি ব্যবহৃত হয় [চিত্র : ৩.২(ত)]। অপটিক্যাল স্কয়ারের মতো একই নীতিতে তৈরি এবং একই কাজে ব্যবহার হয় অপটিক্যাল প্রিজম স্কয়ার। এ ছোট যন্ত্রটি বেশ আধুনিক এবং একক প্রিজমে তৈরি বিধায় এতে সমন্বয়ের দরকার হয় না। এতেও প্রতিফলন পৃষ্ঠ 45° কোণে স্থাপিত । তবে লাইন রেঞ্জার হিসাবেও এটি ব্যবহার করা যায়। এতে ধুলাবালি আটকানোর সুযোগ নাই।
(ট) হোয়াইটস্ (Whites) :
এগুলো বাঁশ বা কাঠের তৈরি, সচরাচর মাঠ থেকেই সংগৃহীত। যখন কার্যক্ষেত্রে রেঞ্জিং রড বা স্টেশন চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি না থাকে বা যখন সাধারণ খুঁটি বা পোল সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন 40 সেমি থেকে 1 মিটার দৈর্ঘ্যের কাঠ বা বাঁশের খণ্ডের এক প্রান্ত সুচালো ও অপর প্রান্ত কিয়ৎ পরিমাণ চিরে এতে সাদা কাগজ লাগিয়ে স্টেশনে পুঁতে দেয়া হয়। ফলে স্টেশন সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষ করে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত স্থানে কন্টুর বিন্দু চিহ্নিতকরণে এগুলোর ব্যবহার দেখা যায় ।
আরও দেখুন: