শিকল বা ফিতা দিয়ে রৈখিক দূরত্ব পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “সার্ভেয়িং ১” বিষয়ের “শিকল জরিপের কার্যপ্রণালি” বিভাগের একটি পাঠ।
Table of Contents
শিকল বা ফিতা দিয়ে রৈখিক দূরত্ব পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া

যেহেতু নকশা প্রণয়নে অনুভূমিক পরিমাপের দরকার হয়, তাই শিকল বা ফিতা দিয়ে কোনো রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপকালে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে রেখাটি সমতলে (অনুভূমিক তলে) আছে কি না। ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল (অনুভূমিক) হয় তবে এতে কোনো রেখার দৈর্ঘ্য মাপলে সরাসরি অনুভূমিক মাপ পাওয়া যাবে। আর যদি ভূপৃষ্ঠ ঢালু বা বন্ধুর হয় তবে সরাসরি পরিমাপ নিলে অনুভূমিক মাপ পাওয়া যাবে না। তাই সঠিক জরিপ এবং অনুভূমিক তলে সঠিকভাবে পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয় এবং নক্শা অঙ্কনের উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে জরিপ রেখার রৈখিক দূরত্ব পরিমাপ করা হয় ।
(ক) সমতলিক ভূমিতে রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া :
রেখার দৈর্ঘ্য যদি এক শিকল দৈর্ঘ্যের কম হয় তবে দু’ স্টেশনের মধ্যকার দূরত্ব সহজেই মাপা যায়। এক্ষেত্রে অনুগামী (follower) প্রারম্ভিক স্টেশনে শিকল বা ফিতার হাতল ধরে রাখবেন এবং অগ্রগামী (Leader) সামনের স্টেশন পর্যন্ত স্বাভাবিক টানে ফিতা বা শিকল রেখে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ জেনে নেবেন।
আর যদি শিকল রেখা বেশ দীর্ঘ হয় তবে অনুগামী শিকল বা ফিতার হাতল প্রারম্ভ স্টেশনে শক্তভাবে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চেপে ধরবেন এবং অগ্রগামী 10টি তীর (arrow) 1টি রেঞ্জিং রড ও শিকল বা টেপের হাতল ধরে সামনের দিকে শিকল রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে শিকল বা টেপের পূর্ণদৈর্ঘ্য পুরা হবার প্রাক্কালে তার হাতের রেঞ্জিং রড় উল্লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে পিছনের দিকে তাকাবেন এবং অনুগামী প্রারম্ভিক স্টেশনের রেঞ্জিং রড ও প্রান্তীয় স্টেশনের রেঞ্জিং রড তাক করে অগ্রগামীর রেঞ্জিং রড অগ্রগামীর মাধ্যমে ডানে-বামে করে একই সরল রেখায় আনবেন অর্থাৎ পঙক্তিকরণের কাজ শেষ করবেন।
এরপর অগ্রগামী পঙক্তিকৃত রেখায় শিকল বা টেপ স্বাভাবিক টানে টান করে শিকলের প্রান্তে একটা তীর বসিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং রেঞ্জিং রড, তীর (৭টি) ও শিকলের (ফিতার হাতল ধরে (বসানো তীরের একটু দূর দিয়ে) সামনের দিকে অগ্রসর হবেন, যেন বসানো তীর স্থানচ্যুত না হয়। অনুগামীও শিকলের হাতল ধরে তাকে অনুসরণ করবেন এবং সামনের তীরের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ‘শিকল বা টেপ’ বলে চিৎকার করে অগ্রগামীকে থামিয়ে দিয়ে তিনি পূর্বের মতো তার হাতের রেঞ্জিং রড পুঁতবেন এবং অনুগামী পূর্বের মতো পঙক্তিকরণের কাজ শেষে তীরের সাথে লাগিয়ে শিকল ধরবেন এবং অগ্রগামী শিকল বা টেপ টান টান করে প্রান্তে তীর বসাবেন।
এ সময় অনুগামী প্রথম শিকলের প্রান্তীয় তীর উঠিয়ে নিবেন। এভাবে রেখার প্রান্ত পর্যন্ত রৈখিক দূরত্ব পরিমাপের কাজ চলতে থাকবে। 10 শিকল মাপার পর অনুগামীর হাতে 10টি তীর জমা হবে এবং অগ্রগামীর হাতে কোনো তীর থাকবে না। এরপর অনুগামী সব তীর (10টি) অগ্রগামীর হাতে ফেরত দিবেন ।

(খ) ঢালু বন্ধুর ভূমিতে রেখার অনুভূমিক দৈর্ঘ্য পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া :
বন্ধুর ভূমিতে কোনো রেখার অনুভূমিক দৈর্ঘ্য দু’পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়, যথা-
১। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ও
২। পরোক্ষ পদ্ধতি।
১। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ঃ
এ পদ্ধতিতে প্রতিবারে শিকল বা ফিতার পুরো দৈর্ঘ্যে পরিমাপ নেয়া হয় না বরং ভূমির ঢাল এবং শিকল বা ফিতার ওজনের উপর ভিত্তি করে এদের 10, 20 বা 30 একক করে মাপতে হয়।

এক্ষেত্রে অনুগামী (follwer) শিকলের প্রান্ত রেখার (AB) উঁচু প্রান্তে (A) ধরে এবং অগ্রগামী (Leader) শিকল বা ফিতার নির্দিষ্ট দূরত্বে (dj) ধরে এটাকে পরিমিত টানে টান টান করে বিনা ঝুলনে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে ওলন ঝুলিয়ে ভূমিতে ওলনের স্পর্শ বিন্দু (A) চিহ্নিত করে। এরপর অনুগামী চিহ্নিত বিন্দুতে (A)) শিকলের প্রান্ত ধরে এবং অগ্রগামী শিকল বা ফিতার নির্দিষ্ট দূরত্বে (d) ধরে এটাকে পরিমিত টানে টান টান করে বিনা ঝুলনে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে ওলন ঝুলিয়ে ভূমিতে ওলনের স্পর্শ বিন্দু (A2) চিহ্নিত করে।
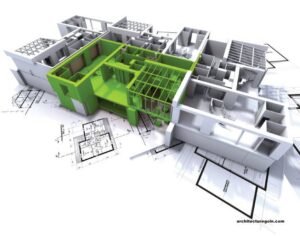
এভাবে ঢালের রেখার সমাপ্তি বিন্দু (B) পর্যন্ত মাপ নেয়া হয় এবং পরিমাপকৃত সকল অনুভূমিক দৈর্ঘ্য (d), d2, d3…) যোগ করলে A B রেখার অনুভূমিক দৈর্ঘ্য (D) পাওয়া যায়। যেহেতু ধাপে ধাপে পরিমাপ নেয়া হয়, তাই এ পদ্ধতিকে ধাপ পদ্ধতিও বলা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়–
(i) পরিমাপ উপরের দিক হতে নিচের দিকে করতে হবে।
(ii)ঢালের মাত্রা ও শিকল বা ফিতার ওজনের উপর ভিত্তি করে প্রতিবারের দৈর্ঘ্য পরিমাপের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।
(iii) দূরত্ব যতই কম নিতে হোক না কেন অগ্রগামী (Leader) কোনোক্রমেই চক্ষু উচ্চতার অধিক উচ্চতায় শিকল বা ফিতা ধরতে পারবে না ।
(iv) ওলন ঝুলানো কালে শিকল বা ফিতাকে অবশ্যই অনুভূমিক অবস্থায় রাখতে হবে ।
(v) মাপ নেয়ার কালে শিকল বা ফিতায় ঝুলন (Sag) হতে পারবে না।
২। পরোক্ষ পদ্ধতি :
এ পদ্ধতিতে এবনি লেভেল বা ক্লিনোমিটারের সাহায্যে ঢালের কোণ [Angle of slope (0)] মাপা হয় এবং ঢাল বরাবরে দৈর্ঘ্যের মাপ (L) নেয়া হয়। এরপর সূত্রের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। (চিত্র ৫.৫) অনুভূমিক দূরত্ব, D = Lcose

আরও দেখুন:
