কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “সার্ভেয়িং ১” এর “কিস্তোয়ার জরিপের প্রাথমিক ধারণা এর ব্যবহারিক” পাঠ এর অংশ।
Table of Contents
কিস্তোয়ার জরিপে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা
মুরব্বী (Quadrilaterals) :
কিস্তোয়ার জরিপে জরিপের সুবিধার্থে একটি মৌজাকে কতগুলো চতুর্ভুজ আকৃতির অংশে বিভক্ত করতে হয়। এ অংশগুলোর প্রত্যেকটিকে মুরব্বা বা চতুর্ভূজ বলা হয়। এ চতুর্ভুজ বা মুরব্বার কোনায় কোনায় স্টেশন করা হয়, এ স্টেশনগুলোকে মোরব্বা স্টেশন বলা হয়। মোরব্বার বাহুর দৈর্ঘ্য 10 হতে 14 শিকল (গান্টার) হয়ে থাকে। মৌজার সরু দিক হতে মোরব্বা তৈরির কাজ আরম্ভ করতে হয়। এতে ভুলের পরিমাণ কম হয়। প্রতি মোরব্বা স্টেশনে 60 সেমি হতে 120 সেমি ব্যাসের (2 ফুট থেকে 4 ফুট) বৃত্ত কেটে চিহ্নিত করতে হয়। মোরব্বা রেখা যেখানে কোনো জমির আইলকে ছেদ করে, তার মাপ খাতায় লেখতে হয়। নক্শা তোর কালে মোরব্বা রেখায় কালি দিতে হয় না।
কাটান (Intersection) :
মুরব্বা রেখা বা শিকল রেখা যে স্থানে কিত্তার আইল অর্থাৎ জমির আইল, রাস্তা, খালকে ছেদ করে, তাকে কাটান বলে। কাটানের দূরত্ব থাকায় লেখতে হয়। থাকায় ছোট ছোট দাগ দিয়ে কাটানগুলো চিহ্নিত করতে হয় এবং মাটিতে দাগ কেটে দিতে হয় ।
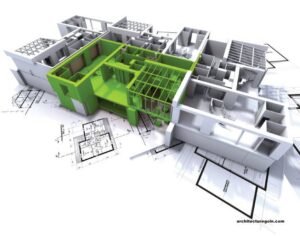
রিপে প্রতিটি মুরব্বার জমির প্লটগুলোকে নিখুঁতভাবে নক্শায় উঠানোর জন্য মোরব্বাস্থ বেশিরভাগ প্লটগুলোর লম্বালম্বি আইলের মোটামুটি সমান্তরাল করে দু’শিকল অন্তর অন্তর যে-সব রেখা টানা হয়, সেগুলোকে সিকমি বা সিকমি রেখা বলা হয়। অপটিক্যাল স্কয়ারের সাহায্যে সিকমি রেখার সাথে অফসেট নিয়ে জমির প্লটগুলো নক্শায় উঠানো হয়। তবে মূল নক্শায় সিকমি রেখা থাকে না এবং এগুলোতে কালিও দেয়া হয় না। চান্দা (Chanda) : কিস্তোয়ার জরিপে ঘের জরিপের স্টেশন ও ত্রিসীমানা বিন্দুগুলোকেও মুরব্বা স্টেশন হিসেবে ধরা হয়। এসব স্টেশন বাদে জরিপের সুবিধার্থে আরো কিছু অস্থায়ী স্টেশনও নেয়া হয় এবং এগুলোকে 30 সেমি ব্যাসের বৃত্ত কেটে ভূমিতে (বিশেষ করে জমির আইলে) চিহ্নিত করা হয়— এগুলোকে চান্দা বলা হয় ।
পরতাল রেখা (Check line) :
কিস্তোয়ার জরিপ চলাকালে আমিনের কাজ অর্থাৎ জরিপ কাজ বিশুদ্ধভাবে হচ্ছে কি না তা যাচাই করে দেখার জন্য নক্শার আড়াআড়ি কোনো রেখা বা কোনো দু’বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সরাসরি মাঠে পরিমাপ করে নক্শার সাথে মিল আছে কি না দেখে নেয়া হয়। একে পরতাল বলা হয় এবং যে রেখার দৈর্ঘ্য সরজমিনে মাপা হয়, তাকে পরতাল রেখা বলা হয়। পরতাল রেখার দৈর্ঘ্য ৪ থেকে 25 শিকল পর্যন্ত হতে পারে, তবে সাধারণত 15 থেকে 20 শিকলই নেয়া হয়।
মাঠ থাকা (Field Khaka) :
প্লেন টেবিল বা থিওডোলাইটের মাধ্যমে তৈরি ঘের নক্শা বা স্কেলিটন ম্যাপ (P-70 Sheet) মা ব্যবহারের জন্য নিতে হয়। ফলে অধিক ব্যবহারের ফলে এটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ট্রেসিং করে এটার অনুলিপি তৈরি করে মাঠ ব্যবহার করা হয় । এ হাত নক্শাকে মাঠ থাকা বলা হয়। এটাকে থাকাও বলা হয় ।

মৌজা :
কিস্তোয়ার জরিপের সময় উপজেলাধীন যে ভৌগোলিক এলাকা পৃথক পৃথক পরিচিতি নম্বরে আলাদা করা হয়, তারে মৌজা বলে। গ্রাম, পাড়া ইত্যাদি মৌজার আওতাধীন এলাকা এবং জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার একক হলো মৌজা । জে.এল. নম্বর ঃ উপজেলা/থানার অধীন মৌজাগুলোকে পর্যায়ক্রমে ক্রমিক নম্বরে চিহ্নিত করা হয়। পরিচিতিমূলক মৌজার ও – নম্বরকে জে.এল. নম্বর বা জুরিসডিকশন লিস্ট নম্বর বলা হয়।
নকশা শিট :
বৃহৎ মৌজার নকশা একই কাগজে প্রণয়ন করা সম্ভব না হলে একাধিক কাগজে খণ্ডে খণ্ডে মৌজা নকশা প্রণয়ন করতে হয়। মৌজা নকশার আলাদা আলাদা প্রতিটি খণ্ডকে নকশা শিট বা সাধারণভাবে শিট বলা হয়। একটি মৌজার শুধুমাত্র একটিই নকশা হয়, তবে মৌজার আকার বড় হলে একটি নকশার জন্য একাধিক নকশা শিট থাকতে পারে।
তৌজি :
কালেক্টরেটে (১৮০০ সালের ৮নং রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী) প্রত্যেকটি জমিদারির জমির তফসিলসহ খাজনার বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে একটি রেজিস্টার খোলা হয়। এ রেজিস্টার তৌজি রেজিস্টার নামে পরিচিত এবং এগুলোর ক্রমিক নম্বর তৌজি নম্বর নামে পরিচিত। জমিদারের জোতজমা এলাকা, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদির বিবরণকে তৌজি বলা হতো ।

ভূমি রেকর্ড :
ভূমি (আবাদি, অনাবাদি জমি, বাড়িঘর, বাগান, জঙ্গল, বনভূমি, জলমগ্ন এলাকা ইত্যাদি) সংক্রান্ত টেকনিক্যাল রুলস্, এস.এস. ম্যানুয়াল, সার্ভে আইন, প্রজাস্বত্ব আইন ও বিধিমালা মোতাবেক ভূমি নকশা এবং ভূমি মালিকানার বিবরণ লিপিবদ্ধ
করা হয়। ভূমি মালিকানার খতিয়ান (Records of rights) এবং নকশাকে একত্রে ভূমি রেকর্ড বলা হয় ।
খতিয়ান :
মৌজায় এক বা একাধিক মালিকের জমির বিবরণ যে নির্ধারিত ফর্মে (৫৪৬২-সংশোধিত) পৃথক পরিচিতি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাকে খতিয়ান বলে। খতিয়ানে মালিকের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, খতিয়ান নম্বর, জে.এল. নম্বর, স্বত্বের বিবরণ, হিস্যা, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ, শ্রেণি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।
পর্চা :
ভূমি রেকর্ড প্রস্তুতের পর খতিয়ানের অনুলিপি মালিকের নিকট বিলি করা হয়। খতিয়ানের এ অনুলিপিই পর্চা। দাখিলা ঃ তহসিল অফিস হতে ভূমির খাজনা প্রাপ্তির যে রশিদ নির্দিষ্ট ফর্মে দেয়া হয়, তাকে দাখিলা বলা হয় । (ফর্ম নম্বর ১০৭৭)।
তফসিল তালিকা :
জমাজমি হস্তান্তরের দলিলের নিম্নভাগে লিখিত জমির তালিকাকে তফসিল বলা হয়। তফসিলে মৌজার নাম, জে.এল. নম্বর, জমির দাগ নম্বর, পরিমাণ, দাগের চৌহদ্দির দখলদারের নাম উল্লেখ করতে হয়।
পাট্টা :
ভূমির মালিকপক্ষ (জমিদার বা সরকার) ভোগ দখলের অধিকার প্রদানের জন্য রায়ত বা প্রজাকে জমির পরিমাণ ও খাজনা উল্লেখ করে যে অধিকারপত্র দিতেন, তাকে পাট্টা বলে।
ইজারা :
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাজনা নির্ধারণ করে কোনো তালুক বা মহলাদির বন্দোবস্ত গ্রহণ বা প্রদানকে ইজারা বলা হয় । দাগ ঃ একক স্বত্ব বা একক মালিকানাধীন এক চৌহদ্দির একই ধরনের ভূমিকে দাগ (Plot) বলে ।
দাগ নম্বর :
বিভিন্ন মালিকের বা একই মালিকের বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত জমিকে নকশায় যে পৃথক পৃথক পরিচিতি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ নকশায় প্রতিটি দাগকে যে নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাকে দাগ নম্বর বলা হয়।
ছুট দাগ :
খানাপুরি কালে ভুলক্রমে কোনো দাগের খানাপুরি না হলে এতে দাগ নম্বর পড়ে না, এ দাগকে ছুট দাগ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে আমিন ছুট দাগ সম্পর্কে নোট লিখে রাখবেন এবং সকল দাগের খানাপুরি শেষে খসড়ায় যে শেষ দাগ নম্বর পড়বে তার অব্যবহিত পরবর্তী নম্বর ছুট দাগের নম্বর দিতে হবে। নকশার পার্শ্বে এ ছুট দাগ নম্বরে নোট দিতে হবে।
বাটা দাগ :
কোনো দাগকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে নতুন দাগ সৃষ্টি হলে সৃষ্ট দাগকে বাটা দাগ বলা হয়। নকশার উপর কোনোরূপ বাটা দাগ নম্বর হবে না। তবে খসড়া ও খতিয়ানে বাটা দাগ নম্বর হবে। বাটা দাগের নম্বর ভগ্নাংশে হবে, এতে লব নম্বরটি বাটা দাগের পার্শ্ববর্তী দাগের নম্বর এবং হর নম্বরটি খসড়ার শেষের নম্বরটির অব্যবহিত পরের নম্বরটি হবে। নকশার পাশে বাটা দাগ নম্বরের নোট দিতে হবে।
থোকা লাইন :
মৌজা নকশায় কোনো মৌজার ত্রিসীমানা পিলারের নিকট এক শিকল হতে পাঁচ শিকল লম্বা যে রেখা অঙ্কন করে অন্য মৌজার সীমানা দেখানো হয়, তাকে থোকা লাইন বলা হয় ।
খানাপুরি :
কিস্তোয়ার জরিপের মাধ্যমে পি-৭০ শিটে মৌজা নকশা তৈরির কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মাঠ পর্যায়ের কর্মচারী (বিশেষ করে সরদার আমিন) ভূমির স্বত্বাধিকারীদেরকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ২৬ ধারা অনুযায়ী খানাপুরি রেকর্ড বা প্রাথমিক রেকর্ড তৈরি করেন। এ ধাপে আমিন সংশ্লিষ্ট মৌজার প্রত্যেকটি প্লটে গিয়ে নির্দিষ্ট প্লটের মালিক ও জমির বিবরণ খতিয়ান ফর্মের নির্ধারিত কলামের (খানা/ঘর) ঘরে পূরণ (পুরি/পূরণ) করেন। এ বিবরণের মধ্যে থাকে মৌজার নাম, জে.এল. নং, উপজেলা/থানার নাম, জিলার নাম, মালিক/মালিকানার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, মালিকানার ধরন, হিস্যা, দাগ নম্বর, দাগের ক্ষেত্রফল, জমির শ্রেণি ইত্যাদি। খতিরীন ফর্মের নির্ধারিত খানা বা ঘর পূরণ করে বিধি মোতাবেক জরিপ কর্মচারী (আমিন) সে প্রাথমিক রেকর্ড তৈরি করে, তাকে খানাপুরি বলা হয়।
বুঝারত :
পি-৭০ শিটে তৈরিকৃত নকশার ভিত্তিতে প্রাথমিক রেকর্ড তৈরি করার পর রেকর্ড কপি করে পর্চা (খতিয়ানের অনুলিপি) ভূমি স্বত্বাধিকারীদের নিকট বিলি করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বা নোটিশ দিয়ে জরিপ কর্মচারী সরেজমিনে গিয়ে ভূমি মালিকদেরকে রেকর্ড ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। ভূমি মালিকদেরকে সরেজমিনে রেকর্ড ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়ার এ প্রক্রিয়াকে বুঝারত বলা হয় ।
তসদিক বা অ্যাটেস্টেশন :
বুঝারত সমাপ্তির পর বিধি মোতাবেক প্রজাদেরকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে মৌজাওয়্যারি প্রজাস্বত্ব ২৮ বিধি অনুযায়ী বুঝারত ধাপে তৈরিকৃত রাজস্ব রেকর্ড রাজস্ব অফিসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন অফিসার সত্যায়িত করেন। এ সময় রাজস্ব অফিসার পূর্ববর্তী বিভিন্ন রেকর্ড, দলিলপত্র, মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেন এবং মালিক বা মালিকদের বিভিন্ন আপত্তি শ্রবণ করে প্রয়োজনে পর্চার ভুলত্রুটি সংশোধন বা মীমাংসা করে দেন, একে অ্যাটেস্টেশন (Attestation) বা তসদিক বলা হয়। এ সময় নকশার ভুলত্রুটিও সংশোধন করে দেয়া হয়। এ সময় খতিয়ানে অ্যাটেস্টেশন অফিসার স্বাক্ষর ও সিল দিবেন। তবে পর্চাতে শুধুমাত্র সিল দেয়া হবে। তসদিকের পর রেকর্ডের আইনগত ভিত্তি রচিত হয়।
নামজারি বা মিউটেশন :
কোনো ব্যক্তি ভূমির মালিকানা অর্জন করলে (তসদিকের পর) তার নামে খাজনা বা কর দেয়ার সুবিধার্থে বিধি মোতাবেক সরকারি রেকর্ড সংশোধন করে বর্তমান মালিকের নাম রেকর্ডভুক্তকরণের আইনানুগ প্রক্রিয়াকে নামজারি (Mutation) বলা হয়। নামজারি পদ্ধতি রেকর্ড আপ-টু-ডেট করার একটি প্রক্রিয়া। সাধারণত (ক) ভূমির মালিকের মৃত্যুর কারণে উত্তরাধিকারের নাম রেকর্ডভুক্তকরণে (খ) বিক্রি, দান, হেবা, ওয়াকফ, অধিগ্রহণ, নিলামক্রয়, বন্দোবস্ত ইত্যাদি কারণে নতুন মালিকের নাম রেকর্ডভুক্তকরণে (গ) কোনো ভূমির মালিকস্বত্ব বিলোপ করে খাস খতিয়ানভুক্তকরণে নামজারির দরকার হয়।
জমা খারিজ :
যৌথ খতিয়ান হতে কোনো মালিকের হিস্যা (অংশ) পৃথক করে আলাদাভাবে পৃথক খতিয়ানভুক্ত করাকে জমা খারিজ বলা হয়। যৌথ খতিয়ানের মালিকগণকে শুনানি এবং প্রয়োজনে তদন্ত করে খারিজ করতে হয়। জমা খারিজের ফলে খাজনা বা করদানের সুবিধা হয়।
তফসিল :
জমি চিহ্নিতকরণের জন্য জমির অবস্থান, পরিচিতির বিবরণকে তফসিল বলা হয়। তফসিলে মৌজার নাম, জে.এল. নম্বর, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর ও জমির চৌহদ্দির বিবরণ থাকে।
থাক সার্ভে :
লাখেরাজ ভূমি বাদে অন্যান্য জমির কর ধার্য করার জন্য এবং প্রত্যেক মৌজার মধ্যবর্তী লাখেরাজ ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে কালেক্টরি রেজিস্টারভুক্ত করে তৌজি স্থাপনের জন্য যে জরিপ করা হয়েছিল, তাকে থাক সার্ভে বলা হয়। এ জরিপে ভুল ছিল বলে পরবর্তীতে রেভিনিউ সার্ভে শুরু করা হয়। থাক বা মাটির ঢিবি তৈরি স্টেশন করে এ জরিপ করা হয়েছিল বলে একে থাক সার্ভে নামকরণ করা হয়।
রেভিনিউ সার্ভে :
এ জরিপের দ্বারা প্রত্যেক মৌজার সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। যে-সকল এলাকা (এস্টেট বা মহাল) স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল এগুলোর বাউন্ডারি চিহ্নিতকরণে ১৮১২ সাল হতে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যে সার্ভে করা হয়েছিল, তাকে রেভিনিউ সার্ভে বলা হয়। যে-সকল এলাকা আগে স্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল না তাও রেভিনিউ সার্ভের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল এবং এ সার্ভের নকশা 4 = 1 মাইল স্কেলে করা হয়।
পেটি সার্ভে :
নতুন জেগে উঠা চরকে দ্রুত বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য কালেক্টরেটের সার্ভেয়ার দিয়ে বিনা ট্র্যাভার্সে নকশা তৈরি করানো হতো। বিভিন্ন ক্ষুদ্র এলাকায় এরূপ অপ্রমাণিত জরিপকে পেটি সার্ভে বলা হতো। এ ধরনের জরিপ নকশাকে চিটা ম্যাপ বা চর্চা ম্যাপ বলা হতো ।
আরও দেখুনঃ
